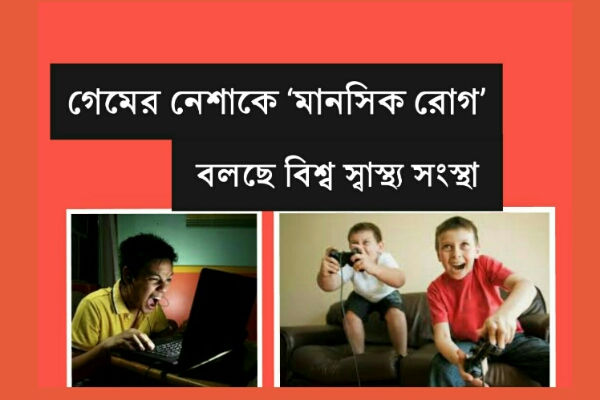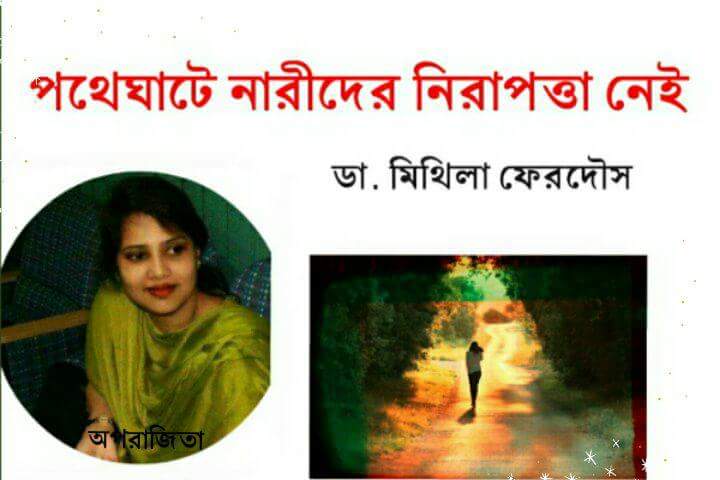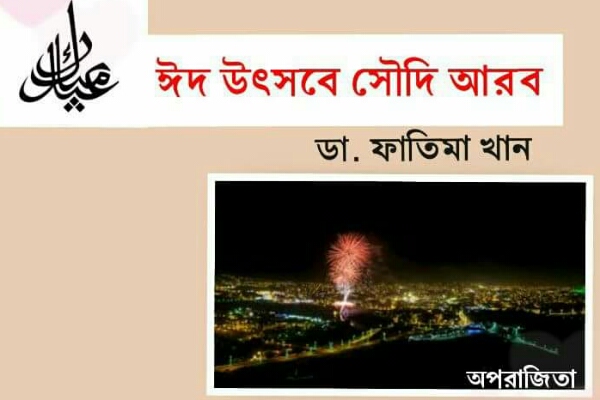রায়হান আতাহার
কিশোর বয়সে যে লেখকদের লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, তার মধ্যে মুহম্মদ জাফর ইকবালের নাম সবার আগে স্মরণ করতে হয়। স্যারের লেখা ‘কিশোর উপন্যাসসমগ্র ১’ আমার সংগ্রহে থাকা সেরা বইগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমগ্রটিতে ছয়টি কিশোর উপন্যাস ছিলো- ‘হাতকাটা রবিন’, ‘দীপু নাম্বার টু’, ‘দুষ্টু ছেলের দল’, ‘আমার বন্ধু রাশেদ’, ‘টি-রেক্সের সন্ধানে’ ও ‘জারুল চৌধুরীর মানিকজোড়’। প্রতিটি উপন্যাস যেন এক একটি ভালোবাসার নাম। কতবার করে যে পড়েছি উপন্যাসগুলো!
সিনেমার পর্দায় ‘দীপু নাম্বার টু’ দেখার পর মুগ্ধতা যেন আরো বাড়লো। সেসময় ইটিভিতে ধারাবাহিকবাভাবে ‘হাতকাটা রবিন’-এর সিরিয়াল দেখাতো। চোখের সামনে ভাসে এখনো। ‘জারুল চৌধুরীর মানিকজোড়’-ও টিভিতে দেখাতো। আর ‘আমার বন্ধু রাশেদ’-এর চলচ্চিত্রায়ন তো এই সেদিনের কথা। ‘টি-রেক্সের সন্ধানে’ ও ‘দুষ্টু ছেলের দল’-কেও হয়তো কোন এক সময় টিভির পর্দায় দেখতে পাবো।
এরপর স্যারের যে বইটি হাতে এল তা হল ‘বেজি’। একই সাথে সাইন্স ফিকশন আর এডভেঞ্চার। সাইন্স ফিকশনের প্রতি আগ্রহ জন্মানোর জন্য এই একটি বই যথেষ্ট ছিলো আমার জন্য। এরপর সাইন্স ফিকশন সমগ্র কিনেছিলাম। দিন নেই, রাত নেই; সাইন্স ফিকশন নিয়ে পড়ে থাকতাম। পরবর্তীতে ম্যাথ অলম্পিয়াডে অংশগ্রহণের জন্য স্যারের গণিত নিয়ে লেখা বইগুলোও পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে।
মুহম্মদ জাফর ইকবাল স্যার আমার চাইল্ডহুড হিরো। তাঁর লেখাগুলো যেন ঠিক আমার মত মানুষদের জন্যই লেখা। কিশোর বয়সের মুগ্ধতা বজায় আছে এখনো। সুযোগ পেলেই তাঁর লেখা পড়ি। তাঁকে নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা আছে, সেদিকে যাবো না। আমার কিশোর বয়সকে রঙিন করার জন্য স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ আমি।
জাফর ইকবাল স্যারের লেখার প্রতি ছোটবেলা থেকে যে ভালোলাগা ছিলো, হুমায়ূন আহমেদের লেখার প্রতি ততটা ভালোলাগা ছোট থেকে ছিলো না। হুমায়ূন আহমেদের লেখার সাথে পরিচয় হয়েছিলো ছোটবেলায় “বোতল ভূত” বইটির মাধ্যমে। বইটির অনেকগুলা গল্পের মাঝে একটি গল্পের চরিত্র ছিলো ‘পিপলী বেগম” নামের একটি পিঁপড়া – এখনো মনে আছে। এরপর কেন যেন তাঁর লেখা পড়া হয়নি ছোটবেলায়।
একটু বড় হয়ে (সম্ভবত নবম শ্রেণিতে) পড়লাম “হিমু রিমান্ডে”। এক অদ্ভুত নেশা পেয়ে বসলো এরপর থেকে। হুমায়ূন আহমেদের কতগুলো গল্প-উপন্যাস পড়েছি আমার নিজেরও জানা নেই। হার্ডকপিতো পড়েছি, সফটকপিও কম পড়িনি। তখন রিভিউ লেখার অভ্যাস ছিলো না বলে কাহিনীও ভুলে গেছি অনেকগুলোর।
“জোছনা ও জননীর গল্প”, “বহুব্রীহি”, “জীবনকৃষ্ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল”, “দেয়াল”, “তেতুল বনে জোছনা”সহ স্যারের অসংখ্য সৃষ্টি দাগ কেটে গেছে মনের ভেতর। তিনি অসংখ্য নাটক-সিনেমা উপহার দিয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে লেখক হুমায়ূন আহমেদকেই বেশি ভালো লাগে। অতি সাধারণ জিনিসগুলোকেও অসাধারণ করে তোলার এক অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলেন মানুষটি। হিমু, রূপা, মিসির আলী, শুভ্র, বাকের ভাইদের মাঝে তিনি বেঁচে আছেন এবং থাকবেন সবার মাঝে।
(চলবে)
Raihan Atahar
Postgraduate Researcher at Bernal Institute
Material and Metallurgical Engineering at BUET