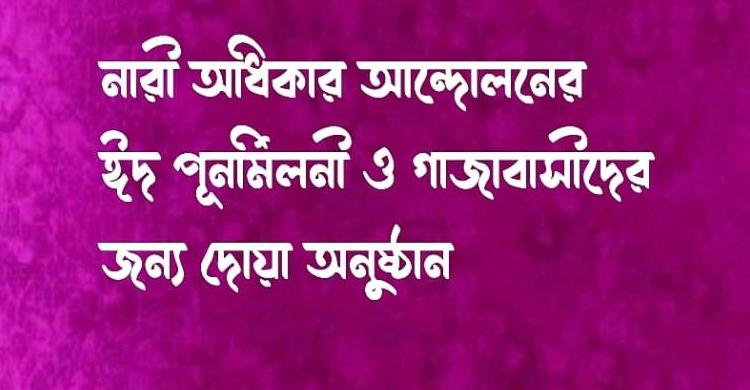বাংলাদেশ উন্নয়নের এক ক্রমবর্ধমান পথে হাঁটছে—এই কথা আমরা প্রতিদিন শুনি, দেখি, পড়ি। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের ২০২৪ সালের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স অনুযায়ী বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় লিঙ্গ সমতায় শীর্ষে এবং বৈশ্বিকভাবে ৯৯তম অবস্থানে রয়েছে। জিডিপির প্রবৃদ্ধি এখন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ঊর্ধ্বমুখী। তবে এই অগ্রগতি ও অর্জনের গর্বের মাঝেই রয়ে গেছে কিছু গোপন, কষ্টকর ও ভয়াবহ প্রশ্ন—এই উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে নারীরা কোথায়? তাদের নিরাপত্তা, অধিকার ও মর্যাদা কি রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে পেরেছে?
বছরের শুরু থেকে বছরের শেষে, ধর্ষণের পরিসংখ্যান প্রতিদিনের সংবাদের এক করুণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৪০১ জন নারী ও শিশু। শুধু জানুয়ারি মাসেই সংখ্যা ছিল ৩৯, আর ফেব্রুয়ারিতে ৪৮। এটি নিছক সংখ্যা নয়—প্রতিদিন ঘটে যাওয়া যন্ত্রণার দলিল। প্রতিটি ঘটনায় কেঁপে উঠে একটি জীবন, একটি পরিবার। সমাজে ধর্ষণ এখন এতটাই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে অনেকেই আর বিস্মিতও হন না—এটা যেন এক ভয়ানক সহনশীলতা তৈরি করেছে।
রাজনৈতিক অঙ্গনে দেখা গেছে কিছুটা পরিবর্তন। দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র ক্ষমতার অবসান ঘটেছে। বিভিন্ন সংগঠন সংস্কারের কথা বলছে, নতুন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে যারা সম্ভাবনার কথা বলছে, বৈষম্যহীন সমাজের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে নারী কি সেই স্বপ্নের অংশ হতে পেরেছে? যৌন সহিংসতা, নারী নিপীড়নের হার কি কমেছে? নারীর নিরাপত্তাবোধ কি বেড়েছে? বরং প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা ও খবরে তার বিপরীতটাই প্রমাণ হয়। ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন এখন শুধু ঘর-বাড়ি বা রাস্তায় নয়, ভার্চুয়াল জগতেও নারীর অস্তিত্বকে ক্রমাগত আক্রমণের শিকার করছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘ভিউ বাড়ানো’ বা ‘ট্রেন্ডিং’ হওয়ার নামে যেসব ভিডিও তৈরি হয়, তার অনেকগুলোতেই নারীর প্রতি অবমাননাকর ও বিদ্বেষপূর্ণ উপস্থাপন রয়েছে। সেইসঙ্গে ততাকথিত ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিলেও নারীকে বস্তু হিসেবে বর্ণনা করে যেসব বক্তব্য দেওয়া হয়, তা শোনে কিশোর-তরুণরা বেড়ে উঠছে একটি ভিন্ন মনস্তত্ত্ব নিয়ে। প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো এসব নিয়ন্ত্রণে কতটুকু সক্রিয়, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এই সমাজে নারী বিদ্বেষ এখন আর গোপন নয়—তা আজ প্রতিষ্ঠিত, স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ধর্ষণ, নিপীড়ন এখন আর লজ্জাজনক বিষয় নয়—বরং ক্ষমতার প্রকাশের এক নোংরা উপায়।
এমন পরিস্থিতিতে যখন একজন ডিএমপি কমিশনার সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন যেন ‘ধর্ষণ’ শব্দটি ব্যবহার না করে ‘নারী নিপীড়ন’ বলা হয়, তখন প্রশ্ন ওঠে—একটি ভয়াবহ অপরাধকে শব্দচয়নের মাধ্যমে কীভাবে হালকা করে দেখানো যায়? ধর্ষণ একটি ফৌজদারি অপরাধ, এবং একে তার প্রকৃত নামে ডাকা উচিত। শব্দের রাজনীতি দিয়ে অপরাধের ভয়াবহতা ঢেকে রাখা যায় না।
এই ক্রমাগত সহিংসতা রোধে শুধু আইনি ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন পরিবারে এমন পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে শিশুরা নির্ভয়ে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারে। শিশুদের জানাতে হবে কীভাবে তারা যৌন সহিংসতার শিকার হতে পারে, কীভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, শিশুদের এসব শেখানো কি ঠিক? কিন্তু বাস্তবতা হলো ধর্ষক কিন্তু কখনো শিশুর বয়স দেখে থামে না। তাই এই লড়াইয়ে শিশুদের অন্ধকারে রাখা মানে তাদের ঝুঁকিতে ফেলে দেওয়া।
নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া, যার জন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ। শুধুমাত্র আইন ও পুলিশ দিয়ে এই ব্যাধিকে দমন করা সম্ভব নয়। প্রয়োজন সমাজে নারীর অবস্থান, মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে নতুন চিন্তা, শিক্ষা ও সচেতনতা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবার, গণমাধ্যম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান—সবকিছুর সমন্বয়ে নারীর মর্যাদার পক্ষে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব জরুরি।
এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত হবে তাদের নিজ নিজ আদর্শিক অবস্থান থেকে নারীর অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ে কার্যকর পরিকল্পনা উপস্থাপন করা। প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে আন্তর্জাতিক লিঙ্গসমতার মানদণ্ড অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে, আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
আমরা আজ এমন এক সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে উন্নয়নকে সত্যিকার অর্থে টেকসই করতে হলে নারীকে নিরাপদ করতে হবে। প্রবৃদ্ধির হার দিয়ে উন্নত রাষ্ট্র হয় না, যদি সেই রাষ্ট্রের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।
বিশ্বাস রাখতে চাই, রাষ্ট্র নারীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নেবে। ধর্ম, গোষ্ঠী, পেশা বা অর্থনৈতিক অবস্থা নয়, রাষ্ট্র তার সাংবিধানিক দায়িত্ব অনুযায়ী প্রতিটি নারী ও কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাসম্পন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করবে।